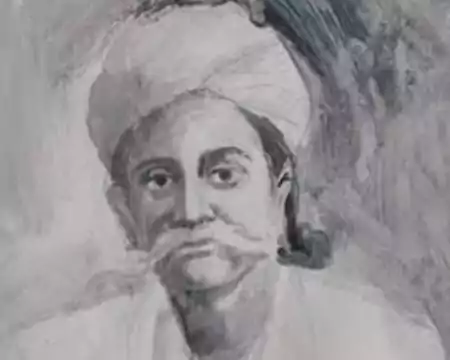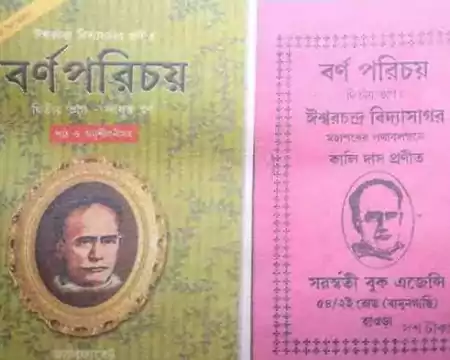চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলাম (লিখেছেন – আব্দুর রহমান আনসারী)
২৯ আগস্ট ১৯৭৬। ঢাকার পি জি হাসপাতাল। ডাক্তার নার্সদের ব্যস্ততা। জীবনমৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছেন। ৭৭ বছর বয়সী নির্বাক, মূক অপলক দৃষ্টির এক মানুষকে বাঁচানোর লড়াই। না হেরে গিয়েছিল গোটা হাসপাতাল। অমোঘ মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেই মানুষটিকে। তারপর সবটাই ইতিহাস। বাংলাদেশ বেতার তরঙ্গে সমগ্র বিশ্ব জানাল দীর্ঘ ৩৪ বছর নির্বাক, মূক অপলক দৃষ্টি…